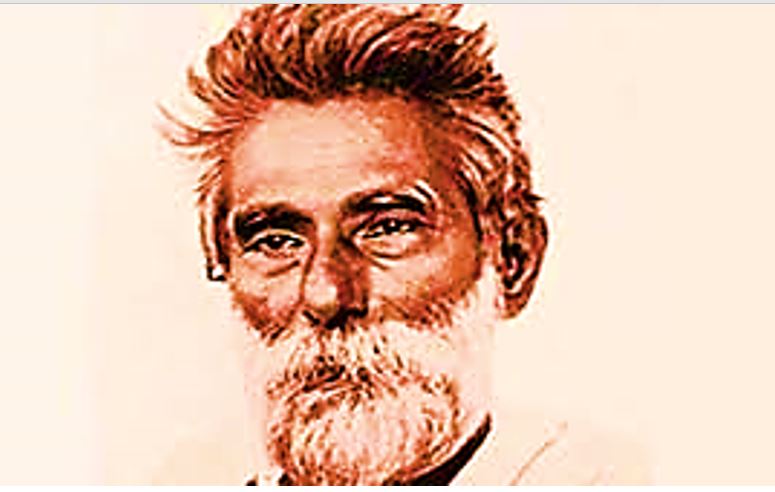রবীন্দ্রনাথ এই গোটা সিন্ধু সভ্যতার একটা আত্মপরিচয় তার প্রবন্ধে এমন করে লিখলেন যা একমাত্র মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ দ্বিমত করল না। তিনি লিখলেন, ‘তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই’।
অর্থ্যাৎ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হলে কিংবা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেই সে আরব কিংবা ইউরোপের ইতিহাস সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে না, সে আসলে ‘হিন্দুই’ থাকে। ভারতের মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন… সকলেই আসলে এই সভ্যতার সন্তান, তারা সকলে ‘হিন্দু’। এই হিন্দু মানে পুজাআচ্চা জপতপ ব্রত পালন করা কোন সনাতন ধর্মালম্বী নন। এমন কি এই ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের একমাত্র ‘হিন্দু’ ভেবে বসে থাকলেও যে কিছু যায় আসে না সেটাও রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই; কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশাই হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন। তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন। তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীস্টান। খ্রীস্টান তাঁহাদের রঙ, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে। হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে ‘হিন্দু নও হিন্দু নও’ বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে ‘হিন্দু নই হিন্দু নই’ শুনাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান’।
রবীন্দ্রনাথ ব্লগ-ফেইসবুকে এসব লিখলে আজ তাকে ‘হিন্দুত্ববাদ আরএসএস শিবসেনার এজেন্ট’ এরকম গালাগালি শুনতে হতো। তবে এমন নয় যে রবীন্দ্রনাথ এই সত্য আত্মপরিচয় তুলে ধরার জন্য আক্রান্ত হননি। প্রগতিশীল থেকে মার্কসবাদী কেউ তাঁকে রেহাই দেননি। ‘মুসলমান’ আলাদা স্বতন্ত্র এক জাতি সত্ত্বা। সে ‘হিন্দু’ নয়। কোথা থেকে সে এলো, কে তাদের পূর্বপুরুষ- সেই আত্মপরিচয় দেখাতে গেলেই কেন কেবল বাঙালী মুসলমান ফোঁস করে উঠে? সলিমুল্লাহ খান উপরোক্ত রবীন্দ্র প্রবন্ধ পাঠ করে বলেন, ‘ভারতের বৃহৎ হিন্দুজাতি- খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন সবাইকে হিন্দু বানাইতে চায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলিতেছিলেন, মুসলমানরা একমাত্র বেয়াদব, যাহারা হিন্দু পরিচয় স্বীকার করিবে না’।
না, সলিমুল্লাহ খানদের পূর্বসূরীরাও তা স্বীকার করতে চাননি। তারা এতখানি ভদ্র ছিলেন না তাই রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুত্ববাদী, হিন্দু ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা, সাম্প্রদায়িক মানুষ, সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু (প্রিন্স অফ ওয়েল্সের সম্মানে গান লিখেছেন), মুসলমানের প্রতি বিরূপ ইত্যাদি বলে খিস্তি করে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা সংবাদপত্রে একের পর এক প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। প্রেক্ষাপট ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের আয়োজন হয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তানে। সে বছর রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানে স্মরণ করতে ঢাকায় সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে তিনটি কমিটি গড়ে উঠল। বাংলা একাডেমি সরকারী প্রতিষ্ঠান বলে রবীন্দ্র জয়ন্তী থেকে বিরত থাকল। সাহিত্যিক লেখকদের উদ্যোগে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মুরশেদকে সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের রিডার খান সারওয়ার মুরশিদকে সম্পাদক করে প্রথম কমিটি গঠিত হয়। দ্বিতীয়টি গঠিত হয়েছিলো কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে এবং তৃতীয়টি প্রেসক্লাব থেকে। বুদ্ধিজীবীদের এই অংশটিই ৯০ দশক পর্যন্ত প্রগতিশীল সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। সেই ১৯৬৭ সালে যখন রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো তখন এই বুদ্ধিজীবীরাই সারাদেশে তীব্র প্রতিবাদের মাধ্যমে দেশের মধ্যে অন্য রকম এক বাঙালী জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিলেন। বলাই বাহুল্য এই জাগরণের কেন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধের প্রতিবাদে বিবৃতি দেন মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, জয়নুল আবেদিন, সুফিয়া কামাল, মালিক আবদুল বারী, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, খান সারওয়ার মুরশিদ, সিকানদার আবু জাফর, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আহমদ শরীফ, নীলিমা ইব্রাহিম, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও শহীদুল্লা কায়সার।
লেখকদের নামের তালিকায় বিশেষ করে ড. আহমদ শরীফের নামটি মনে রাখুন। আমরা পরবর্তীতে দেখব তিনি এক ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের সামনে। আমরা বরং তারও আগে থেকে রবীন্দ্র বিদ্বেষ নিয়ে আলোচনা করে নেই। পাকিস্তান আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী বিখ্যাত লেখক আবুল মনসুর আহমদ তার ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’ বইতে রবীন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করে লিখেছিলেন, ‘হাজার বছর মুসলমানরা হিন্দুর সাথে একদেশে একত্রে বাস করিয়াছে। হিন্দুদের রাজা হিসেবেও, প্রজা হিসেবেও। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই হিন্দু-মুসলমানে সামাজিক ঐক্য হয় নাই। হয় নাই এই জন্য যে, হিন্দুরা চাহিত আর্য-অনার্য, শক, হুন যেভাবে ‘মহাভারতের সাগর তীরে’ লীন হইয়াছিল, মুসলমানেরাও তেমনি মহান হিন্দুসমাজে লীন হইয়া যাউক। তাহারা শুধু ভারতীয় মুসলমান থাকিলে চলিবে না, ‘হিন্দুমুসলমান’ (হিন্দুরূপী মুসলমান) হইতে হইবে। এটা শুধু কংগ্রেসী বা হিন্দুসভার জনতার মত ছিল না, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও মত ছিল’।
অর্থ্যাৎ মুসলমান এই ভূমির কেউ নয়? চরমোনাই পীর কিছুদিন আগে পল্টনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, মুসলমানের ইতিহাস হেন্দুর ইতিহাস নয়, মুসলমান উমার উসমানের বংশধর, শাহ জালাল শাহ পরানের বংশধর…। আজকাল সত্যি বলতে কি, এই বঙ্গের কয়েক শতকের ইতিহাস পাঠ করে আমি এখন আর আহমদ শফী, মুফতি ফয়জুল্লাহদের সঙ্গে এই লেখায় উল্লেখিত ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন তফাত পাই না। আশ্চর্য যে, চিরকাল এই ইসলমাপন্থিদের কাজকে সহজ করে দিয়েছে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা! ১৯৪৮ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভবানী সেন কমিউনিস্টদের জন্য সাংস্কৃতিক তত্ত্ব (ফতোয়া) দেন যাতে রবীন্দ্রনাথকে প্রগতিবিরোধী বুর্জোয়া হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাকে বর্জন করার ঘোষণা দেয়া হয়। এই তত্ত্বকে স্বাগত জানান মুনীর চৌধুরী, আখলাকুর রহমান, আবদুল্লাহ আল-মুতী, আলাউদ্দিন আল আজাদ। যদিও মুনির চৌধুরী ১৯৬৭ সালের রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধের প্রতিবাদে যে বিবৃতি সাক্ষর হয় তাতে নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পাকিস্তান হবার পর পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের জয়জয়কার। পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের রবীন্দ্র বিরোধীতা, তাকে পরিত্যাগের কাজটি সহজ হয়েছিলো যখন মুনীর চৌধুরী, আখলাকুর রহমান, আবদুল্লাহ আল-মুতী, আলাউদ্দিন আল আজাদ মত প্রভাবশালী লেখকরা রবীন্দ্র বিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন। সেই ভূমিতেই দাঁড়িয়ে লেখক সৈয়দ আলী আহসান বললেন, আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত। আমরা যেমন বর্তমানকালে দেখি মার্কসবাদীরা আমেরিকার বিরোধীতায় হামাস হিজবুল্লাহর মত জিহাদী দলগুলোকে পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে বসে- চিরকালই তাদের স্থান কাল সম্পর্কে কোন বুদ্ধি বিচার দেখি না। তাদের বুদ্ধি আছে আক্কেল নেই! একটা আত্মপরিচয় সংকটে থাকা ধর্ম সম্প্রদায় যখন তার জাতিসত্ত্বা অন্বেষণ করছে তখন রবীন্দ্র বিরোধীতার সময়টিকে কাজে লাগিয়ে ফের তাকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের সন্ধান দিতে তৎপর গ্রুপটি তার সুযোগ নিয়েছে। ৬৭ সালে বাঙালী শিক্ষিতরা তাদের ছেলে মেয়েদের নাম বাংলাতে রাখা শুরু করেছিলো। ছায়ানটে শাড়ি পরে রমনায় গান শুনতে যাওয়া, ঢাকার রাস্তায় প্রভাবফেরিতে নারীর দীপ্ত উপস্থিতি, সেই ভর পাকিস্তান আমলে এদেশের নারীরা যখন ঘোমটা ছাড়া রাজপথ কাঁপাচ্ছে, দেশ স্বাধীন হবার একদম গোড়াতে, যে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী মুসলমানকে দ্বিজাতি তত্ত্ব থেকে ফের নিজের সত্ত্বায় ফিরিয়ে আনলেন, লড়াই করে যে বাঙালী রবীন্দ্রনাথকে অর্জন করল, হঠাৎ ১৯৭৩ সালে আহমদ শরীফ বাংলা একাডেমীর উত্তরাধিকার পত্রিকায় ‘রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র-মূল্যায়ন’ প্রবন্ধে লিখলেন, ‘তিনি ব্রাহ্মদের হিন্দু আখ্যা দিয়েছেন এবং আস্থা স্থাপন করেছেন প্ল্যানচেটে; প্রাচীন পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে এবং বৌদ্ধ, রাজপুত ও শিখ আখ্যান নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন, কিন্তু মুসলিম শাসক ও দরবেশ নিয়ে কিছু লেখেন নি – তাতে মনে হয়, মুসলমানদের প্রতি তিনি বিদ্বিষ্ট ছিলেন অথচ ইংরেজ শাসকদের প্রতি তাঁর অপরিমেয় অনুরাগ, গভীর আস্থা ও নিবিড় শ্রদ্ধা দেখা যায়; তাঁর গল্পে-উপন্যাসে গণমানবের স্থান হয়নি, তিনি তাদের কল্যাণকামী ছিলেন না; তাঁর মনের গভীরে ছিল সামন্তবাদের প্রতি মোহ অথচ উপনিবেশে তাঁর ঘৃণা ছিল না; তিনি জমিদারি উচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন, নিজেও ছিলেন নিপীড়ক জমিদার’। এইরকম ভাবে রবীন্দ্রনাথকে অংকন করে তিনি সিদ্ধান্তে আসলেন ‘রবীন্দ্র-সাহিত্য আর আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে না…’।
আহমদ শরীফের এই রবীন্দ্র বিরোধীর মূলে ছিলো উনার মার্কসবাদী অবস্থান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করা সবক’টি অভিযোগের কোনটিই আহমদ শরীফ প্রমাণ করতে পারেননি। আনিসুজ্জামান লিখেছেন, প্রজার নিপীড়নের অভিযোগটির কোন ভিত্তিই পাওয়া যায়নি। আহমদ শরীফও তার কোন প্রমাণ দেননি। হায়াৎ মামুদ আহমদ শরীফের এই লেখার তীব্র প্রতিবাদ করে পরের সংখ্যায় উত্তরাধিকারে লেখেন, হায়াৎ মামুদের সেই লেখা এবং আহমদ শরীফের লেখা সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ দানে পরাঙ্মুখ কিংবা সাম্প্রদায়িক কিংবা অত্যাচারী জমিদার ছিলেন বলে যে-দাবি করা হয়েছে, তাঁর (আহমদ শরীফ) জানা তথ্য (যদিও সেসব তথ্যের বিবরণ তিনি দেননি) তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। পাশ্চাতের আটজন লেখক ও দার্শনিকের উল্লেখ করে তিনি (হায়াৎ মামুদ) বলেন, কারো ব্যক্তিগত জীবন ও শিল্পসিদ্ধি পৃথকভাবে গণ্য করা দরকার এবং এ-দুয়ের মধ্যে সৃষ্টিশীলতার প্রশ্নটিই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, রবীন্দ্রনাথ কেন মার্কসবাদী হলেন না বা সমাজপরিবর্তনের দায় স্বীকার করেন নি কেন কিংবা তাঁর রচনায় মুসলিম-চরিত্র কেন অনুপস্থিত, এসব প্রশ্ন বর্তমান প্রজন্মের জন্যে প্রাসঙ্গিক নয়। তিনি পাঠকদের মনে করিয়ে দিলেন যে, যাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে, তিনি নিজের পার্থিব ও পরিবেশগত সীমা ছাড়িয়ে একটি সংস্কৃতিকে তার শ্রেষ্ঠ রূপ দান করেছিলেন’। পরবর্তীতে আহমদ শরীফের ঐ লেখার সমালোচনা করে আরো লেখেন শওকত ওসমান, খান সারওয়ার মুরশিদ, শামসুর রাহমান, হুমায়ুন আজাদ। সৈয়দ শামসুল হক আহমদ শরীফের ঐ রচনাকে বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথের জন্মের একশ পঁচিশতম বার্ষিকীতে বাংলাদেশে আমাদের সবচেয়ে কলঙ্কিত কাজ’!
আমরা যখন বাংলা ব্লগের শুরুর দিকে লিখতে আসি তখন দেখতাম শিবিরের ব্লগাদের তীব্র রবীন্দ্র বিদ্বেষ। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ বিরোধীতা করেছিলেন। অথচ বাংলা ভাগ না হলে পাকিস্তান হতো না, আর পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না। তাহলে এতদিন পর্যন্ত কোলকাতার দাদাবাবুদের, দিল্লির বড় বাবুদের পা টিপে জীবন চালাতে হতো ইত্যাদি। পরবর্তীকালে মুক্তমনা ব্লগেও দেখলাম জাতীয়তাবাদী ব্লগারদের রবীন্দ্র এলার্জি। দেখলাম মার্কসবাদী ব্লগারদের রবীন্দ্র বিদ্বেষ। অথচ আমরা চরমোনাই পীরের ভাষণ শুনে ছি: ছি: করে উঠি। এখন দেখছি ঠক বাছতে গাঁ উজাড়! রবীন্দ্রনাথ হিন্দুত্ববাদী! রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক! রবীন্দ্রনাথ মুসলিম বিদ্বেষ! অথচ আমাদের মনে রাখতে হবে হিটলার শাসিত জার্মানিতে রবীন্দ্র রচনাবলী নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। মুসলিম জাতীয়তাবাদী পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ হয়েছিলো। কমিউনিস্টরা রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছিলো। নকশালরা তাঁর মূর্তি ভেঙ্গেছিলো। তাঁর লেখা গানকে জাতীয় সংগীত মানতে চায় না মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা। এতে রবীন্দ্রনাথের কিছু যায় আসে না। বরং রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়ের সন্ধানকে গ্রহণ না করে রক্তের স্রোতধারায় দেশভাগ হয়। হাজার হাজার নিরপরাধ নারী যারা রাজনীতি বুঝে না ধর্ষণের শিকার হয়। কোটি কোটি মানুষ নি:স্ব হয়ে দেশছাড়ে। ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করে মাশুল দেয় ৩০ লক্ষ মানুষ। ধর্ষিতা হয় নারী। শরণার্থী হয় অগুণতি মানুষ…।
আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ তাই কেবল কবি সাহিত্যিক নন, তিনি এক মহান দার্শনিক। যিনি আমাদের আত্মপরিচয়ের পথ দেখান। শত শত ধর্ম জাতি সংস্কৃতি নিয়ে যে জটিল উপমহাদেশ- রবীন্দ্রনাথ তার শান্তির দুত মাত্র। আমরা যতবার রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করেছি ততবার নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছি…।
…………………………
তথ্যসূত্র: রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ, আনিসুজ্জামান, কালি ও কলম, রবীন্দ্র সার্ধজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা।/আত্মপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী/ পূর্ব বাঙলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, বদরুদ্দীন উমর, প্রথম খণ্ড/ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, আবুল মনসুর আহমদ, পৃষ্ঠা ১৫৮-১৫৯/ সাম্প্রদায়িকতা, সলিমুল্লাহ খান, দৈনিক বণিক বার্তা, ২০/১০২০১২)।